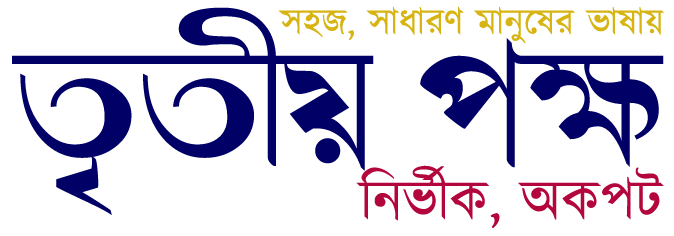কেরি ও আমার আড্ডাপর্ব
তুষ্টি ভট্টাচার্য
মেন বিল্ডিং-এ বাংলা ক্লাস। বাংলা মানে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। ইলেভেনের সায়েন্স। কারুর মন নেই, স্যার পড়িয়ে যাচ্ছেন…ওগুলো বাংলা? মানেই বুঝতে পারছে না বেশিরভাগ। মানে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কেউ শুনলে তো? একে তো কম্পালসারি অপশোনাল সাবজেক্ট…যা হোক করে কিছু লিখে দিলেই পাস্। কে আর আর্টস সাবজেক্ট নিয়ে মাথা ঘামায় তখন! নিতান্ত অ্যাটেন্ডেন্সের ভয়ে এসে বসা। গল্পগুজব হচ্ছে বিনবিন করে, হাই তুলছে অনেকেই। বিশাল হলঘরের অর্ধেকটা পার্টিশন করে বেঞ্চ পেতে দেওয়া হয়েছে এই ক্লাসরুমে। বিরাট উঁচু সিলিং থেকে লম্বা রডে ফ্যান ঘুরছে। মোটা মোটা দেওয়ালের ভেতর, রোদ না-আসা এই ঘরে ঠাণ্ডায় ঘুম এসে যাচ্ছে অজান্তে। ঝিমোতে ঝিমোতে ক্লাসের প্রায় শেষে এসে চারলাইন কানে এলো—চর্যাপদ থেকে বলছেন স্যার।
ওগ্গর ভত্তা রম্ভয়া পত্তা
গাইকো ঘিত্তা দুগ্ধ সযুক্তা
মইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিচ্ছই কন্তা খা পুনবন্তা।
চর্যাপদে মাছের কথা উল্লেখ রয়েছে, এটুকু বেশ বোঝা গেছিল সেদিন। আর এরপরেই আমাদের সমবেত ঝিমুনি, বকবকানি থেমে গেছিল এক ঝটকায়। স্যার তখন কেরির ছড়া বলতে শুরু করেছেন-
উইলিয়াম কেরি তার ‘ইতিহাস মানা’র একটি ছড়া বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। ছড়াটির বিষয়বস্তু ‘কৃষকপত্নীর গণনায় মাছের হিসাব।’
এক কৃষক চাষ করতে গিয়ে কোনো খালে গোটা চব্বিশেক মাছ ধরে বাড়ি এসে তার স্ত্রীকে মাছ রাঁধতে দিয়ে আবার চাষের ক্ষেতে চলে গেল। কৃষকপত্নী যথাসময়ে রান্না শেষ করে মাছ রান্না কেমন হলো পরখ করতে একটি মাছ চেখে দেখল। এর পর আরেকটি মাছ খেয়ে স্বাদ পরীক্ষা করে সে সন্তুষ্ট হতে চাইলে ‘এই রূপে খাইতে খাইতে একটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিল।’ বাড়ি ফিরে একটি মাছ পাতে দেখে কৃষক বিস্মিত হয়ে বাকি মাছের কী হলো, জানতে চাইলে তার স্ত্রী মাছের হিসাব বুঝিয়ে দিল এভাবে:
মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা (৪ঢ৬ = ২৪)
চিলে নিলে দুগণ্ডা (৪ঢ২ =৮)
বাকি রহিল ষোল।
ধুতে আটটা জলে পলাইল,
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়
তবে থাকিল দুই।
আর একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই।
তবে থাকিল এক;
এখন হইস যদি ভালো মানুষের পো,
কাটাখানা খাইয়া মাছ খান থো।
ছড়াটি দাম্পত্য জীবনের ওঠা-নামারও একটি মিষ্টি মধুর ব্যঙ্গমাখা উপাদেয় ছড়া। যোগীন্দ্রনাথ সরকার তার সংকলিত ‘খুকুমণির ছড়া’য় এ মজার ছড়াটি হিসাব শেখানোর উদ্দেশ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।
নিমেষে আমরা চাঙ্গা হয়ে গেছিলাম, অন্তত আমি। ক্লাস শেষ হয়ে গেছিল এরপরেই। টিফিনের পনেরো মিনিটের ব্রেক মাত্র। এরই মধ্যে আমাদের খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি। মেনবিল্ডিং-এর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চোখে পড়ল কেরির সমাধির দিকে। রোজই তো দেখি…আজ একটু বেশিক্ষণই দেখলাম। খোলা মাঠের গাছের ছায়ায় কয়েকটা ছেলে বসেছিল। ওদের পেরিয়ে আসতে গিয়ে পিছন থেকে আওয়াজ শুনলাম…ডিংডং ডিং, চার, পাঁচ, ছে…গারা, বারা… বুঝলাম কিছুটা। লাল টপের সঙ্গে সাদা ঘের দেওয়া স্কার্ট পরেছি, তখনকার মাধুরী-ফ্যাশন অনুযায়ী। কান না দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি আর গোপা। ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছি এরপরই। ভাগ্যিস্ লক্ষ্য করেননি আমাদের! গোবিন্দবাবু তখন ওই দলটাকে তাড়া করেছেন প্রায়। মাঠে বসে আড্ডা দেওয়া ছিল নিষেধ, স্কার্ট পরা নিষেধ…বাবারে বাবা! এটা কলেজ না গোবিন্দ বাবুর টোল কে জানে! সেযাত্রা সোজা বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে ডুকে আত্মগোপন। তবে ফেরার সময়ে আমাদের স্বভাব অনুযায়ী, মেন বিল্ডিং-এর পিছন গেট দিয়ে ঢুকে, সামনের গেট দিয়ে বেরনোর সময়ে দেখি, কেরির মিউজিয়াম খোলা রয়েছে। গোপাকে বললাম, ‘চল্, ঘুরে আসি একটু। আরামসে চারটে পাঁচের ট্রেন ধরে নেব আর পনেরো মিনিট পরে বেরলে’। গোপার স্বর নিম্নগ্রামে ঘোরাফেরা করে বলে, ওকে অনেকেই শান্তশিষ্ট ভাবে। আসলে ও যথেষ্টই অশান্ত। কেরির মিউজিয়ামে ঢুকতেই দেখি সেই ছেলের দলটাও ওখানে গম্ভীর হাবভাব নিয়ে ঘুরছে। পরে জেনেছিলাম ওদের দলের পান্ডা আকাশ। এবং সেদিন মিউজিয়ামের মতামত লেখার খাতায় ওরা খিস্তি লিখে এসেছিল গুছিয়ে। আর যথারীতি, গোবিন্দবাবুর ঘরে ওদেরই তলব পড়েছিল পরের দিন। নেটওয়ার্ক কত নিখুঁত থাকলে অপরাধী ধরতে সময় লাগে না, সেদিন বুঝেছিলাম। ঠিক এই কারণে গোবিন্দবাবুর নাম শুনলেই আচ্ছা আচ্ছা বদমাশ বাচ্চারা ভয় পেত। ভাইসপ্রিন্সিপাল হয়েও তিনি ছিলেন কলেজের সবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যেন!

যাই হোক, আসল কথায় ফিরি। সেদিন গোপা আর আমি কেরির ছবি, জিনিসপত্র, ইত্যাদি দেখছি ঘুরে ঘুরে। হঠাতই মনে হল, ওই বিশাল হলের একেবারে শেষপ্রান্ত থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে! কেউ যে ডাকছে, শুধু আমাকেই ডাকছে, এটুকু আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম তখন। গোপাকে বললাম, ‘তুই দাঁড়া একটু, আমি ওদিক থেকে আসছি দুমিনিটে’। কী এক টানে পৌঁছে গেলাম হলের শেষপ্রান্তে। এখানটায় কেউ নেই এখন। একটা ধোঁয়াশার মতো অস্বচ্ছতা রয়েছে এখানটায়। কম আলোর জন্যই হয়ত। একজন দীর্ঘদেহী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে। আমি একটু এগোতেই দেখি, একজন সাহেব মৃদু হাসি মুখে নিয়ে আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমিও আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়ালাম। কানে এলো, পরিষ্কার বাংলায় উনি বলছেন, ‘হ্যালো! আমি উইলিয়াম কেরি। তুমি কি আমাকেই খুঁজছ?’ আমি ঘাড় নাড়লাম শুধু। বললাম, ‘বাঃ! আপনি তো দারুণ বাংলা বলেন সাহেব!’ কেরি হাসলেন যেন একটু। তারপর বলে উঠলেন, ‘তোমার জুতোতে সেফটিপিন লাগানো কেন?’ ‘আর বোল না গো! ওই যে ফিজিওলজি ল্যাবের কাছে দেওয়ালের একটা খাঁজ আছে না—ওখানে লুকোতে গেছিলাম। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পট করে স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল’। ‘তা স্ট্র্যাপের আর কী দোষ বল? দুটো মাত্র সরু ফিতে সারা জুতোয়, তায় পেন্সিল হিল্! ধকল সইবে কেন? কিন্তু লুকোতে গেছিলে কেন শুনি?’ ‘ওই যে আমার বন্ধুগুলো আছে…হীরকেরই প্ল্যান যদিও। ব্যাটা ভিটভিটে শয়তান একটা। আমাকে মুরগি করে রামদার দোকানে চাউমিন খাবে ঠিক করেছিল। তাই ছুটির আগেই টুক করে কেটে পড়েছি। কিন্তু এমনই কপাল, জুতোটা গেল ছিঁড়ে। আর সেই অবস্থায় মুখোমুখি হলাম এসএস ম্যাডামের। তিনি তো প্রচুর ঠেস মেরে কথা বললেন। এত্ত রাগ হচ্ছিল…’ এবার সাহেব হোহো করে হেসে বললেন, ‘রাগ হচ্ছিল কেন? কী বললেন উনি?’ ‘একে তো স্বাস্থ্য মন্ত্রীর স্ত্রী, তায় ডিপার্টমেন্ট হেড, সব্বাই ওকে জোহুজুর ভাব দেখায়। এদিকে কী বাজে যে পড়ায়…একদম ভাল্লাগে না আমাদের কারুর। বই দেখে দেখে রিডিং মারে…আমরা ফিকফিক করে হাসি ওর ক্লাসে। এদিকে নিজের গা থেকে শ্যানেলের গন্ধ ভুরভুর করছে, দামী শাড়ি, বিদেশী ঘড়ি…চুলের ছাঁট, কথা বলার ধরন দেখলেই বোঝা যায় এলিট ক্লাস। তাও আমার সাজ নিয়ে পড়েছে! আমাকে বলছে—ব্বাবা! কী জুতো! কলেজ না ফ্যাশন শো? রাগ হবে না বল?’ ‘তা তো একটু রাগ হবেই। যাক, এবার আমাকে তোমার জুতোটা দাও। আমি সারিয়ে দিচ্ছি’। আমি হাঁহাঁ করে উঠলাম। ‘আরে বল কী সাহেব! আমি স্টেশনে গিয়েই সারিয়ে নেব। তুমি এই নিয়ে মাথা ঘামিও না’। ‘তুমি কি জান, আমি একজন মুচি। সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে এই পেশায় আছি’। আমার হাঁ মুখ আরও হাঁ হয়ে উঠল। সাহেব আমার মাথায় একটা হালকা চাঁটি দিয়ে বললনে, ‘তবে পড়াশুনোটাও করেছি কিন্তু! মুচির কাজ করতে করতে সেই বয়সে কত কী শিখেছি! প্রকৃতির পাঠ নিয়েছি। অন্য ভাষা শেখার আগ্রহও সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছে’। আমি মহা আগ্রহে তখন কেরির মুখে তার কথা শুনছি। সাহেব ততক্ষণে কথা বলতে বলতে আমার জুতোটি সারিয়ে দিলেন একেবারে নতুনের মতো করে। ‘আমি নিকোলাসের কাছে কাজ শিখতাম, নিকোলাসও ছিল আমার মতো চার্চম্যান। সেই সময়ে ওই গ্রামেরই এক কলেজ পড়ূয়ার কাছ থেকে আমি গ্রীক শিখে নিয়েছি। নিকোলাস মারা গেলে আমি চলে যাই টমাস ওল্ড নামে আরেক মুচির কাছে কাজ করতে। সেটা ১৭৭৯ সালের কথা। আর তার দু বছর পরে ওল্ডের শালী, ডরোথি প্ল্যাকেটকে বিয়ে করি। আমার বউ ছিল নিরক্ষর। বিয়ের খাতায় নাম সইয়ের জায়গায় সে ক্রুশ চিহ্ন এঁকেছিল। আমাদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মেছিল। যদিও আমার মেয়ে দুটি খুব ছেলেবেলাতেই ঈশ্বরের কাছে চলে যায়। আর ছেলে পিটারও পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। এরপরই ওল্ড মারা গেল। ফলে পুরো ব্যবসার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ল। এই যে এত সংসার জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি বললাম তোমাকে, এরই মধ্যে আমি কিন্তু হিব্রু, ইটালি, ডাচ ও ফরাসি ভাষা শিখে নিয়েছিলাম। জুতো সারাতে সারাতে বা তৈরি করতে করতেই আমি পড়তাম’। ‘বাঃ! দারুণ তো! আচ্ছা সাহেব, আবার কাল আসব, আজ দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন পাব না। চারটে পাঁচ না পেলে টিউশনে লেট হয়ে যাবে’। এই বলে আমি ছুটতে ছুটতে গোপার কাছে চলে এলাম। ভেবেছিলাম ও বুঝি খুব রাগ করবে। কিন্তু কিছুই হয়নি, এমন মুখ করে আমরা স্টেশনের দিকে চললাম। ঘড়িতে দেখি, সময়ও খুব একটা নষ্ট হয়নি। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তাহলে কি কেরির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি? কল্পনায় ভাবছিলাম এসব? কিন্তু আমার ছেঁড়া জুতো সারাই করল কে তবে? আশ্চর্য!

এরপর রোজই আমার আর কেরি সাহেবের আড্ডা হয়। কিন্তু সেকথা কেউই ঘুণাক্ষরে জানতে পারে না। আমি আমার কথা বলি, আর সেও বলে তার কথা। সেদিন যেমন বললাম, ‘এই হলঘরে ছায়া ছায়া অন্ধকারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। চল, বরং আমরা চার্চের পেছনে গিয়ে বসি’। ‘মানে? কোনখানে?’ ‘আরে! তুমি ওই জায়গায়টায় যাওনি এতদিনেও? চল, আমার সঙ্গে। ওই খানে দুদিক থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট বারান্দা মতো রয়েছে। বারান্দাও ঠিক না, চাতালের মতো। ওখানে আমরা মাঝেমাঝেই গিয়ে বসি, আড্ডা দিই, খাওয়াদাওয়া করি’। আমরা ওখানে গিয়ে গুছিয়ে বসলাম এবার। তারপরে আমি শুরু করলাম, ‘জান, কাল কী কাণ্ড! আমার আর গোপার সঙ্গে অঞ্জন আর সোমনাথ একই ট্রেনে ফেরে। ওরাও শেওড়াফুলি নেমে সাইকেল নিয়ে চৌমাথা যায়। তা কাল স্টেশনে নামতেই চেকার অঞ্জনকে ধরল। ওরা তো জীবনেও টিকিট কাটে না। ব্যাটা আমাকে দেখিয়ে বলল, ওর কাছে টিকিট আছে। চেকার যেই আমার দিকে ফিরেছে, ও একদম হাওয়ায় উবে গেল! কী বিচ্ছিরি অবস্থা বল দেখি! আমার অবশ্য মান্থলি থাকে। চেকারও মুচকি হেসে আমায় আর কিছু বলেনি’। কেরি সাহেব বেজায় মজা পেয়ে হোহো করে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর বলতে থাকল, ‘জান তো, তোমাদের এখানে, মানে কলকাতায় আসার জন্য আমাদের বৃটিশরা জাহাজে উঠতে দেয়নি। তখন ডরোথি সন্তান সম্ভাবনা ছিল। ওর বোন কেটিরও আসার কথা ছিল আমাদের সঙ্গে। তারপর অবশ্য এক ড্যানিশ ক্যাপ্টেনের জাহাজে ১৭৯৩ সালের নভেম্বরে আমরা কলকাতায় আসি। এসেই বাংলা শিখতে শুরু করি। আর মদনবাটির এক নীলকুঠিতে ছ’বছর ম্যানেজারের চাকরি করতে থাকি। এর আগে ১৭৯২ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি গঠন করেছিলাম। সেই মিশনারির কাজকর্ম, যেমন বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার, এইসব কাজকর্ম করতাম। যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের প্রতি পদে বাধা দিত। ইংরেজ সরকারের মিশনারি বিতাড়ন এড়াবার জন্য আমরা ডেনিশদের শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিই। এখানে এসে আমি অর্থ তহবিলের ভার নিই এবং বাইবেল অনুবাদের কাজ পরিচালনা করতে থাকি। মার্শম্যান বিদ্যালয় এবং ওয়ার্ড মুদ্রণ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ফাউন্টেনের ওপর ভার পড়ে গ্রন্থাগার গড়ার। ১৮০০ সালের ২৪ এপ্রিল শ্রীরামপুর মিশন চার্চের উদ্বোধন হয়। আমি হলাম চার্চের পুরোহিত এবং মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সহকারী পুরোহিতের ভার নেন। এই মিশন ছিল স্বনির্ভরশীল। মার্শম্যান বিদ্যালয়, ওয়ার্ড প্রেস আর আমি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করে নিজেদের ভরণপোষণ ও মিশনের কাজ চালাতে থাকি’।

‘বাবা! তোমার তো প্রচুর দায়িত্ব ছিল তাহলে!’ আমার এই কথায় ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কেরি। ‘শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কাঠের হরফের ব্লক তৈরি করে ছাপা হত। পরে ধাতুর ইংরেজি ও বাংলা হরফ তৈরি করা হয়। এ সময়ে হরফ তৈরিতে পঞ্চানন কর্মকার বিখ্যাত ছিলেন। আমি তাঁকে মিশনে নিয়োগ করি। মিশনের ছাপাখানার কম্পজিটার ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। কিন্তু এত কিছুর পরেও শেষ রক্ষা হল না। মিশন প্রেসে একদিন আগুন ধরে গেল। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল মারাত্মক। যাক সেকথা আবার একদিন হবে। তোমার খবর কী? আর সেই দুষ্টু ছেলের?’ ততদিনে দুবছর কেটে গেছে। আকাশ অনেক শান্ত হয়ে গেছে। ‘সে অন্য স্ট্রিমে, ফিজিক্সে অনার্স। ওর চেয়ে বয়সে বড় এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। এত বদমাশি সত্ত্বেও ও হায়ার সেকেন্ডারিতে ৮৫% পেয়েছিল কীভাবে সেটাই আমাদের গবেষণার বিষয় ছিল অনেকদিন। ওরই এক সাকরেদ অমিতাভ তো তোমারই লাইনে গেছে। লেদার টেকনোলজি নিয়ে পড়তে যাচ্ছে আগ্রায়। তার আগে আমাদের বায়ো ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল মজা মারতে। আর এর আগে আকাশও অবশ্য হায়ার সেকেন্ডারিতে নতুন আসা ছোটোখাটো চেহারার কম বয়সী এক ফিজিক্সের স্যারকে পিছন থেকে চাঁটি মেরেছিল। তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। নিপুণ ভাবে অভিনয় করে বলেছিল, ও নাকি কোন এক বন্ধু ভেবে এই কাজ করেছে! এরপরে ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টে এক অল্প বয়সী সুন্দরী ম্যাডাম এলেন। ও নাকি তাঁর সঙ্গে একই অটোতে শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে কলেজে এসেছে আর তাঁর প্রেমে পড়ে গেছে। এই কথা সে আবার আমাকেই ফলাও করে জানিয়েছে। ওর নাকি ফিজিওলজি আছে—এই কথা জানিয়েছে ম্যামকে। তাই ওঁর ক্লাসে এসে বসে থাকছে রেগুলার নিজের ক্লাস ছেড়ে। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় সে পালিয়েছে যথারীতি। তবে সত্যি সত্যিই প্রেম করা শুরু করে ও শান্ত হয়েছে আজকাল’। কেরি বলল, ‘তা ভালোই তো। প্রেম মহৎ। ডরোথি তো বড় ছেলে মারা যাওয়ার পরে আর বাঁচলই না। আমার জীবন খাঁখাঁ করত তখন। মিশনের অবস্থাও হয়ে উঠল তথৈবচ’।

‘কেন? কেন? কী হয়েছিল?’ ‘সে অনেক লম্বা ইতিহাস গো মেয়ে। শোন তাহলে। আগেই বলেছি, ১৮১২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড ঘটে। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও প্রেসটি পুনর্গঠিত করা গেছিল যদিও। এরই মধ্যে সুখের কথা ছিল, ১৮১৩ সালে মিশনারিদের ওপর থেকে কোম্পানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এর ফলে মিশনের সামনে কর্মক্ষেত্র প্রসারের বিপুল সুযোগ আসে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে মিশন প্রত্যক্ষভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এভাবে ধীরে ধীরে দেশে নবজাগরণের পথও প্রস্ত্তত হয়। মিশন এ সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে তাদের শাখা স্থাপন করে’। ‘সে তো একদিক থেকে ভালই হয়েছিল তোমাদের’। ‘হ্যাঁ, তা হয়েছিল কিছুটা। দেশীয়দের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালে মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষাদানও এই কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ফলে এই কলেজে দুই ধারার শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ১৮২২-২৩ সালে উইলিয়ম ওয়ার্ড ও আর আমার বড় ছেলে ফেলিক্সের হঠাৎ মৃত্যু হলে মিশন দারুণ সংকটে পড়ে। হুগলি নদীর বন্যায়ও মিশন খুব বিপাকে পড়ে। ডেনিশ সরকারের আনুকূল্যে শ্রীরামপুর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হল। কিন্তু মিশনের বিপর্যয় এ সময় চরমে ওঠে। ১৮২৯-এ শ্রীরামপুর মিশন বাধ্য হয় ইংল্যান্ডের সোসাইটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে। এই মিশন তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন মিশনারি সোসাইটিতে পরিণত হয়। কিন্তু এ সময় কলকাতার যে কোম্পানিতে মিশনের টাকা গচ্ছিত ছিল তা দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে মিশনের জন্য তা অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনে। মিশনের এই দুরবস্থাকালে (১৮৩৪) আমাকেও চলে যেতে হল ইহলোক ত্যাগ করে। মার্শম্যানেরও (১৮৩৭) মৃত্যু হয় এরপর। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে কয়েক বছর চলার পর ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুর মিশন বন্ধ হয়ে যায়’।
সেই ছিল আমার সঙ্গে কেরির শেষ আড্ডা। আমিও ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কলেজ যাওয়ার প্রশ্ন নেই আর। যদিও বহুবার যখনই ওখান দিয়ে গেছি, আজও বুঝতে পারি, আমার বন্ধু কেরি সাহেব আমার জন্য ওই হলঘরের শেষ প্রান্তে আলোআঁধারির মধ্যে আমার জন্যই প্রতীক্ষা করছেন। আমিই বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারিনি, এই হতাশা নিয়ে কলেজ বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে যাই, আসি।